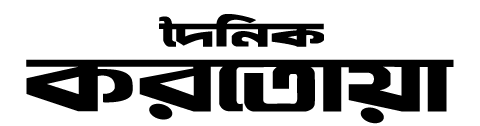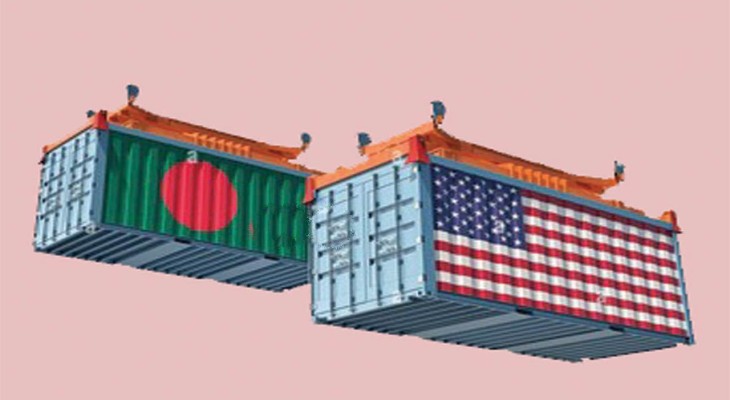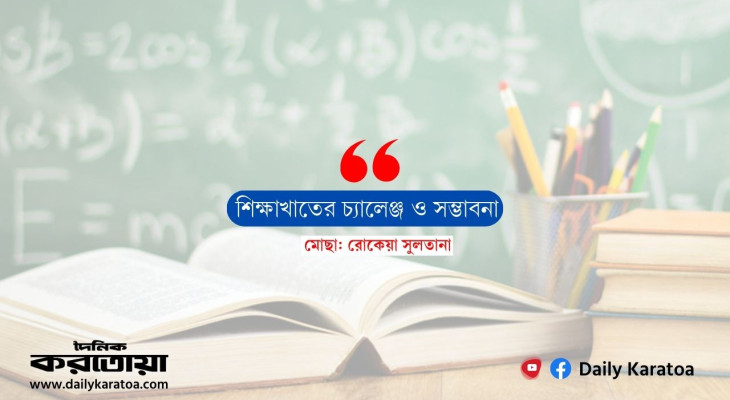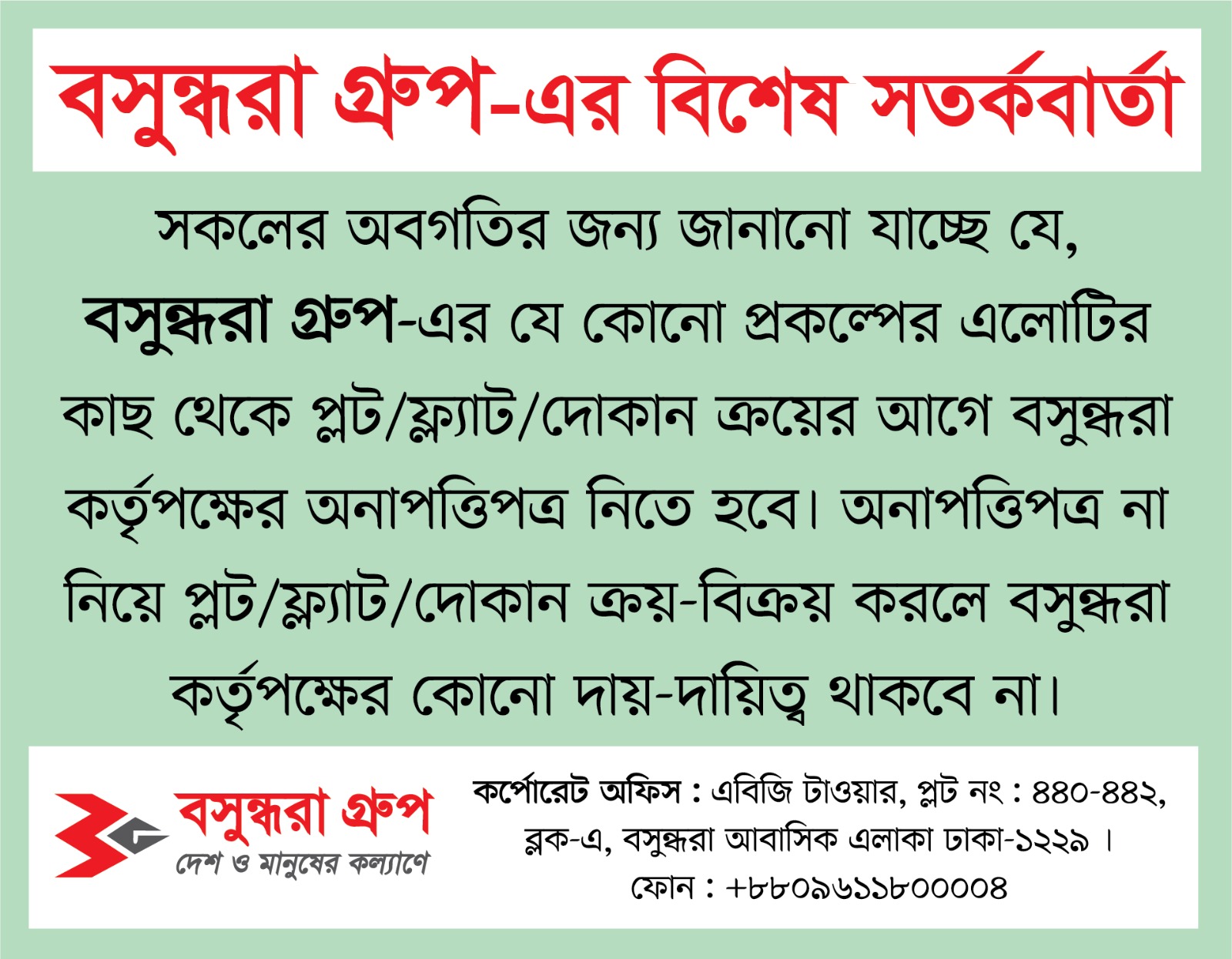শিক্ষাখাতের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা
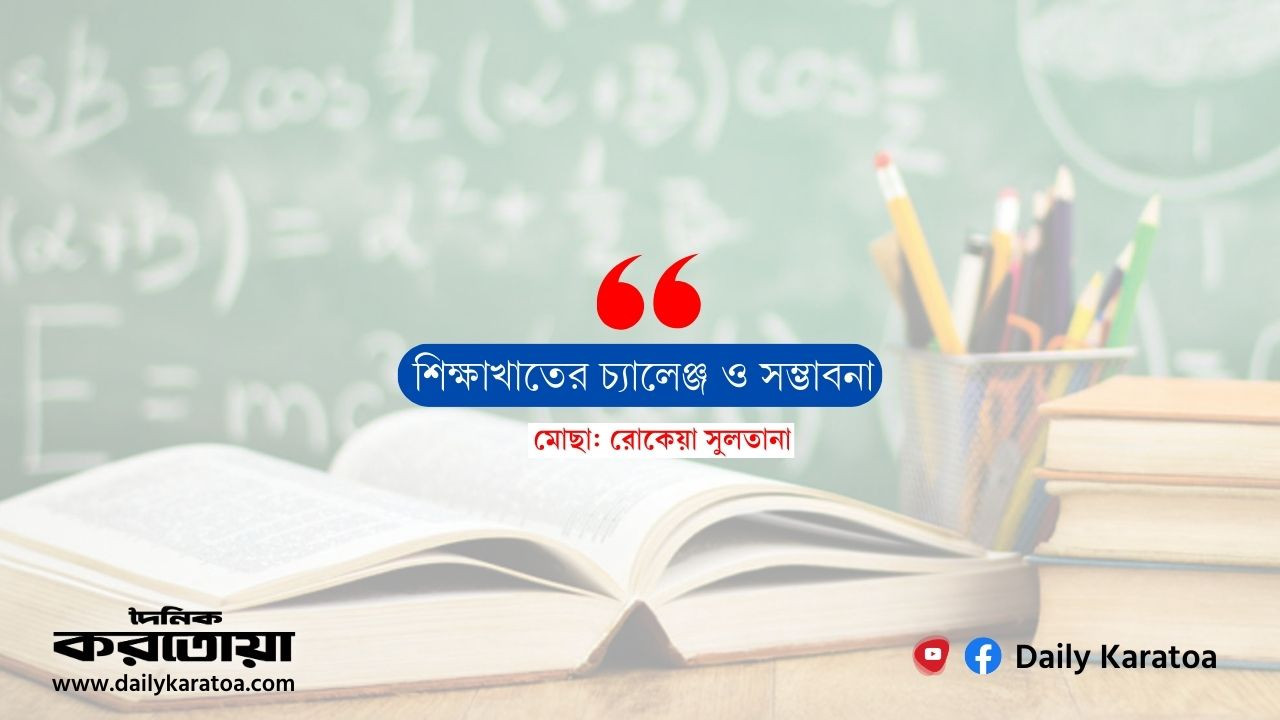
বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন সংকট ও সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। তবে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সরকারের পরিবর্তনের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার পাশাপাশি অসংখ্য চ্যালেঞ্জ সামনে এসেছে। ২০২৪ সালের শেষে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং নতুন সরকারের শাসন শুরু হওয়ায় জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর শিক্ষাখাতে কাক্সিক্ষত সংস্কার বাস্তবায়ন কতটা সম্ভব, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। বাজেট সংকট, জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপান্তর প্রকল্পের স্থবিরতা, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার সম্প্রসারণে ধীরগতি এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামোগত দুর্বলতা এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে না পারলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থায়ী নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে, বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
শিক্ষামন্ত্রণালয়ের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের গতি ধীর হয়ে গেছে। ২০২৩ সালে চালু হওয়া জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপান্তর প্রকল্প ২০২৫ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ নতুন কাঠামো তৈরির লক্ষ্যে কাজ করছিল। কিন্তু প্রশাসনিক পরিবর্তনের কারণে এই প্রকল্পের অগ্রগতি থমকে গেছে। একইভাবে, কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণ কর্মসূচি, যেখানে ১০ লাখ শিক্ষার্থীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল, সেটিও নীতিগত অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে।
অর্থনৈতিক সংকটও শিক্ষাখাতের জন্য বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ছিল জিডিপির মাত্র ২.০৮%, যা দক্ষিণ এশিয়ার গড়ের তুলনায় কম। ইউনেস্কোর সুপারিশ অনুযায়ী, এই বরাদ্দ ৪-৬% হওয়া উচিত। শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ বাড়ানো না হলে গ্রামীণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামো উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে। বর্তমানে দেশের ৪০% সরকারি বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ নেই, এবং ৩৫% শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণের সংকট রয়েছে।
শিক্ষার ডিজিটালাইজেশনেও সংকট স্পষ্ট। ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ দেশের ৫০% প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইন্টারনেট-নির্ভর শিক্ষা কার্যক্রম চালু ছিল। তবে গ্রামীণ ও নিম্নবিত্ত শিক্ষার্থীদের জন্য ডিভাইস স্বল্পতা ও নিম্নগতির ইন্টারনেট বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের মাত্র ৩৫% স্কুলে কার্যকর ডিজিটাল ক্লাসরুম ব্যবস্থা আছে, যা শহর ও গ্রামের শিক্ষার মধ্যে বৈষম্য তৈরি করছে।
মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার নিয়ন্ত্রণ করাও নতুন সরকারের জন্য অন্যতম চ্যালেঞ্জ। ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ এই হার দাঁড়িয়েছে ১৭%, যা দক্ষিণ এশিয়ার গড়ের তুলনায় বেশি। অর্থনৈতিক বৈষম্য, শিক্ষার গুণগত মানহীনতা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি পর্যাপ্ত মনোযোগ না থাকায় এই হার আরও বাড়তে পারে, বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ঝরে পড়ার হার ২০২৫ সালের মধ্যে ২০% ছাড়িয়ে যেতে পারে, যদি সরকার জরুরি ভিত্তিতে কার্যকর পদক্ষেপ না নেয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা যুগোপযোগী সংস্কারের ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। ভারতে "নয়া শিক্ষানীতি (নেপ-২০২০)" কর্মমুখী শিক্ষা, গবেষণা এবং প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে, যা ভবিষ্যতের শ্রমবাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অপরদিকে, বাংলাদেশ এখনো সনদনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থায় আবদ্ধ, যেখানে বাস্তবমুখী দক্ষতার তুলনায় পরীক্ষার ফলাফলের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।
আরও পড়ুনবিশ্লেষকদের মতে, নতুন সরকারের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে কয়েকটি জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া অপরিহার্য শিক্ষাখাতে বাজেট ৪% বা তার বেশি করা, কারিগরি ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা, প্রান্তিক অঞ্চলে ডিজিটাল শিক্ষার সম্প্রসারণে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা, ঝরে পড়ার হার কমাতে শিক্ষাবৃত্তি ও উপবৃত্তি কার্যক্রম বাড়ানো এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি নীতি গ্রহণ করা। শিক্ষাখাতের পুনর্গঠনে সরকার এখনই কার্যকর সিদ্ধান্ত না নিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, "বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য টেকসই শিক্ষা সংস্কার এখন সময়ের দাবি। সরকার যদি স্বল্পমেয়াদি রাজনৈতিক পরিকল্পনার পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষানীতি নির্ধারণ না করে, তাহলে দেশের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হবে। "নতুন বছরে বাংলাদেশের শিক্ষার ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে প্রযুক্তির ব্যবহার, কারিগরি শিক্ষার প্রসার এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা জরুরি।
সরকার, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের মধ্যে সমন্বয় করে একটি স্থিতিশীল শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি করা এখন সময়ের দাবি। শিক্ষার পরিবর্তন শুধু একটি সরকারের দায়িত্ব নয়, এটি পুরো জাতির অগ্রগতির প্রশ্ন।
মোছা: রোকেয়া সুলতানা
লেখক : শিক্ষার্থী ও প্রাবন্ধিক
ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী কলেজ।
মন্তব্য করুন